বুলিংয়ের মৃত্যুচক্র ও আমাদের উদাসীনতা
বুলিংয়ের মৃত্যুচক্র ও আমাদের উদাসীনতা
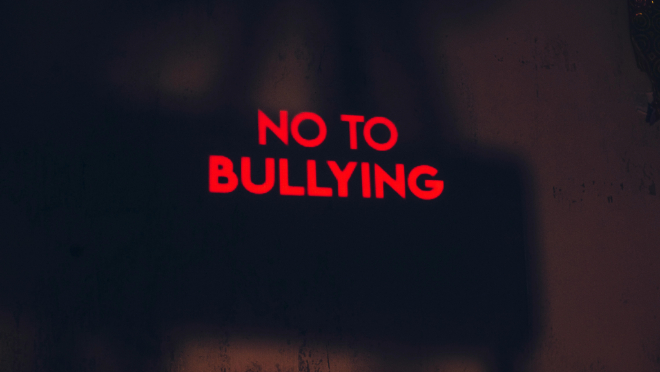
আমরা আসলে কেন বুলিং করি? আর ইস্ট ওয়েস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের ছেলেটার মৃত্যুর কি আদৌ আমাদের টনক নড়াবে?
ছেলেবেলায়, যখন আমি ষষ্ঠ শ্রেণিতে পড়ি, তখন প্রথম শুনেছিলাম, “তোর মতো কালো ছেলের সাথে বন্ধুত্ব করবে কে!” এই একটা বাক্য আমাকে প্রথম শিখিয়েছিল যে এই সমাজের উল্লেখ্য সুশীল মানুষ গায়ের রঙ দেখে, শরীরের গঠন দেখে, পরিবার দেখে এবং এর ওপর ভিত্তি করে পারস্পরিক সম্পর্ক তৈরি করে। হাইস্কুলে প্রথম যেদিন এটা শুনেছিলাম, আমি বুঝলাম সমাজে ‘মানুষ’ হওয়া কখনোই যথেষ্ট না; বরং আমাকে ‘ঠিকঠাক’ মানুষ হতে হবে যেমনটা তারা আশা করে। ঠিক রঙের, ঠিক শরীরের, ঠিক পরিবার থেকে আসা। সেখান থেকে মানসিক অবসাদ তৈরি হয় এবং সেটি কাটিয়ে উঠতে বেশ বেগ পেতে হয় আমাকে।
দুঃখের বিষয়, এত সময় পার হওয়ার পরও কিছুই বদলায়নি। বরং আরও খারাপ হয়েছে। ইস্ট ওয়েস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন শিক্ষার্থীর মৃত্যু যেন আবার মনে করিয়ে দিল আমরা কতটা নিষ্ঠুর হতে পারি। আমরা সবাই জানি বুলিং খারাপ। এটি এক প্রকারের মানসিক নির্যাতন। বুলিংয়ের কারণে মানুষ ভেঙে পড়ে, এমনকি আত্মহত্যার পথ পর্যন্ত বেছে নিতে পারে।তারপরও আমরা থামি না, অথবা আমাদের ভেতরের কোনো দাম্ভিক সত্ত্বা আমাদের থামতে দেয় না।
প্রশ্নটি খুব সহজ: কেন?
শিক্ষিত, ইংরেজিভাষী, মুক্তমনা এবং তথাকথিত “আধুনিক সুশীল” সমাজেও কেন এই একবিংশ শতাব্দীতে এসে বুলিং হয় এবং তার কারণে একজন মানুষ আত্মহননের মতো উদ্যোগ নিতে বাধ্য হয়? তাছাড়া এসব এন্টি-বুলিং সচেতনতা, রঙিন প্রচারণা, সেমিনার, ওয়ার্কশপ – সবশেষে এত আয়োজন ব্যর্থ হয় কেন?
কেন আমরা বুলি করি: শিক্ষা, সুবিধাবাদ, এবং সমাজের ব্যর্থতা
আমরা প্রায়ই ধরে নিই, শিক্ষিত হওয়াই মানুষ হওয়া। কিন্তু ডিগ্রি চরিত্র বদলায় না। ইংরেজি জানা কাউকে সহমর্মী করে না। নেটফ্লিক্স দেখে আধুনিক হওয়া যায়, কিন্তু মন মানবিক না-ও হতে পারে।
ইস্ট ওয়েস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের যেসব ছাত্র ওই ছেলেটিকে “কালো”, “মোটা”, “ভাইব নাই” বলে অপমান করেছিল—তারা কেউ অশিক্ষিত ছিল না। বরং তারা নিজেদের ‘মডার্ন’, ‘লিবারেল’, ‘গ্লোবাল সিটিজেন’ পরিচয়ে গর্বিত।
তাহলে তারা এটা করল কেন? কারণ তারা মানুষ হওয়ার শিক্ষা পায়নি।
তাদের শুধু শেখানো হয়েছে সুবিধা ভোগ করা। Privilege–এর জায়গায় অর্থাৎ “সুবিধাজাত অবস্থান” মানুষকে শেখায় ক্ষমতা কিভাবে নিজের স্বার্থে ব্যবহার করতে হয়, কিন্তু সহমর্মিতা শেখায় না।
যারা বুলিং করে তাদের সাধারণ বৈশিষ্ট্য প্রায় একই: “আমি আলাদা, আমি শ্রেষ্ঠ।” পরিবারের অর্থ, বাবার পদ, শহুরে বেড়ে ওঠা, ফর্সা ত্বক, নিখুঁত ইংরেজি—সবকিছুই তারা মনে করে তাদের নিজের যোগ্যতা। যেখানে যোগ্যতা থাকা উচিত, সেখানে সুবিধাজাত অবস্থান ঢুকে পড়ে। আর সুবিধাজাত অবস্থান যখন নৈতিকতার চেয়ে বড় হয়ে যায়, তখন বুলিং হয় ফল। তারা মনে করে, তাদের ধারণাই চূড়ান্ত। তাদের নিজেরাই একটা স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব।
এই শ্রেণিই সবচেয়ে বেশি ব্যাচমেটকে ছোট করে, অপমান করে, নিরুপায় করে আত্মহত্যার মতো নিষ্ঠুর পরিণতির দিকে ঠেলে দেয়। কারণ তারা জানে কোথায় আঘাত করলে মানুষ ভেঙে পড়ে। বাংলাদেশের প্রায় ৪৪.৪% স্কুল শিক্ষার্থী বুলিংয়ের ভুক্তভোগী এবং ৪৯% শিক্ষার্থী সাইবার বুলিংয়ের শিকার—এগুলো কেবল পরিসংখ্যান নয়, এগুলো নীরব হত্যার চিত্র।
আমাদের সমাজে জবাবদিহিতা নামের কোনো সংস্কৃতি নেই। বাবা-মা সন্তানের মানসিক অবস্থার খোঁজ নেন না, শিক্ষকরা ‘মজা’ বলে এড়িয়ে যান, প্রতিষ্ঠানগুলো ছোট ঘটনা ঢেকে রেখে বড় বিপর্যয়ের পথ তৈরি করে। ফলে বিষাক্ত আচরণ স্বাভাবিক হয়ে যায়। বুলি জানে— “কিছু হবে না। ধরা পড়লেও পার পেয়ে যাব।”
বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়েও ভয়ঙ্কর ঘটনা কম নয়। ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে এক ছাত্রী শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের শিকার হলেও অভিযোগ লুকানো হয়েছিল। অর্থাৎ এন্টিবুলিং নীতিমালা থাকা সত্ত্বেও বাস্তবায়ন দুর্বল।
আমরা বুলিকে প্রায়ই সেলিব্রেট করি। যে ছেলে উচ্চভাষী, দাম্ভিক, বিষাক্ত আচরণ করে, তাকে বলি “আরেহ সেতো আত্মবিশ্বাসী, এসব করলে কিইবা হবে।” আর যার প্রতি বুলিং করা হয়, বন্ধুত্বের নামে তাকে বুঝ দেওয়া হয় “আমরা তো কেবল মজা করছি, কিছু মনে করিস না। এটাই তো বন্ধুত্ব।”
আমার মতে, এই মৃত্যু নিছক কোনো দুর্ঘটনা নয়। এটি বছরের পর বছর ঘটে যাওয়া নীরব হত্যার সর্বোচ্চ রূপ। এই দেশে রঙ, শরীর, ভাষা দেখে বিচার করা হয়। এটি পূর্বানুমানযোগ্য। ছেলেটি মারা গেছে, কারণ আমরা সমষ্টিগতভাবে ব্যর্থ হয়েছি। তার বন্ধুরা ব্যর্থ হয়েছে, ব্যাচমেটগুলো ব্যর্থ হয়েছে, ক্যাম্পাস কর্তৃপক্ষ ব্যর্থ হয়েছে। সর্বোপরি আমরা সমাজ হিসেবে ব্যর্থ হয়েছি। এবং ভয়ংকর বিষয় হচ্ছে, আমরা আবারও ব্যর্থ হব, কারণ কাল ভুলে যাব।
সমাধান কোথায়?
সমাধান মোটিভেশনাল বক্তৃতা, পোস্টার বা প্রচারণা নয়। সমাধান শুরু হয় সৎ কথোপকথন থেকে। যেখানে সরাসরি আমরা একজন-একজন কথা বলি, বুঝি, যোগাযোগের ফাঁক ঠিক করি। মুখের উপর পালটা জবাব দিতে হবে। “মজা”, “দুষ্টামি”, “বন্ধুত্ব” এর নামে হওয়া নিষ্ঠুরতাকে চিহ্নিত করে প্রতিবাদ করতে হবে। প্রকৃত পরিবর্তন সেখান থেকেই শুরু হয়।
আর পরিবার যদি সফলতা, জ্ঞানার্জনের পাশাপাশি সহমর্মিতা শেখায়, তবেই সামগ্রিক উন্নতি হবে।
আর সবচেয়ে বড় কাজ হলো নিজের ভেতরের বুলি-কে খুঁজে বের করা। আমাদের অনেকেই, কখনো না কখনো, কাউকে কষ্ট দিয়েছি, কারো শরীর, ভাষা কিংবা সামাজিক প্রেক্ষাপট নিয়ে।
নিজেকে বদলালে পুরো সমাজের পরিবর্তন শুরু হতে পারে।
বুলিং কোনো ছোট্ট গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ সমস্যা নয়। এটা একটা সামাজিক সংক্রমক রোগ, যেখানে তথাকথিত “শিক্ষিত” শ্রেণি সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত। যার একমাত্র প্রতিকার নিজের ভেতরের আত্মিক ও নৈতিক পরিবর্তন। ইস্ট ওয়েস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের ছেলেটি আমাদের জন্য আরেকটা সতর্কবার্তা।
কিন্তু এরপরেও একটা গভীর প্রশ্ন থেকে যায়। আমরা কি এই ধাক্কা থেকে শিক্ষা নিয়ে মানুষ হবো? নাকি আগের মতোই স্ক্রল করতে করতে পরবর্তী রিলসে চলে যাবো?
Disclaimer: The views and opinions expressed in this article are those of the authors and do not necessarily reflect the opinions and views of TBS Graduates.


