ইমোজি আসলে কী?
ইমোজি আসলে কী?
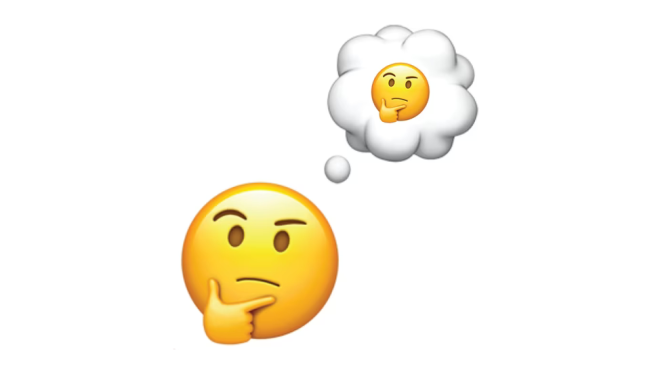
প্রাচীন রোমে একটা বুড়ো আঙুলের ইশারাই ছিল জীবন-মৃত্যুর ফয়সালা। গবেষকরা প্রাচীন ইশারার অস্পষ্ট ইতিহাস ঘেঁটে এমনটাই ধারণা করেন। পরাজিত গ্ল্যাডিয়েটরের ভাগ্য নির্ভর করত সম্রাট বা কোনো উচ্চপদস্থ কর্মকর্তার ওপর, যিনি হয়তো জনতার ইচ্ছাকেই গুরুত্ব দিতেন। মুষ্টিবদ্ধ হাতের ভেতরে বুড়ো আঙুল লুকানো থাকলে তার অর্থ ছিল ‘দয়া করা হোক’। আর বুড়ো আঙুল উঁচিয়ে ধরলে তার মানে ছিল ‘মৃত্যুদণ্ড’।
আজকের দিনে, সেই ‘👍’ ইমোজিটি ঠিক উল্টো পথে হেঁটে ‘সম্মতি’ বা ‘অনুমোদন’ বোঝানোর এক সাদামাটা কিন্তু কার্যকর হাতিয়ারে পরিণত হয়েছে। আবার অনেক সময় এটা যেন শুধু বলে ‘আচ্ছা’, এর বেশি এক বর্ণও নয়।
তবে ইদানীং ইন্টারনেটের দুনিয়া পুরোনো সেই নাটকীয়তাকে নতুন রূপে ফিরিয়ে এনেছে। ইমোজি নিয়ে ইন্টারনেট-সচেতন তরুণ প্রজন্ম তাদের রায় দিয়ে দিয়েছে। তাদের মতে, ‘👍’ ইমোজিটি আর আগের মতো কোনো ইতিবাচক বার্তা দেয় না।
একটি পত্রিকার শিরোনাম ছিল ঠিক এইরকম: ‘জেন জি প্রজন্ম থাম্বস-আপ ইমোজি বাতিল করেছে, কারণ এটি এখন বিদ্বেষপূর্ণ’। আজকের তরুণরা বলছে, কোনো কথার জবাবে শুধু ‘👍’ পাঠানোটা এক ধরনের তাচ্ছিল্য, অসম্মান, এমনকি ‘চরম অভদ্রতা’।
এটা অনেকটা ডিজিটাল মাধ্যমে বিড়বিড় করার মতো, যেন অনিচ্ছাসত্ত্বেও বলা হচ্ছে ‘আচ্ছা, যা বলছ তাই হোক’ বা ‘ঠিক আছে, যা খুশি করো’। এটি যেন এক ধরনের পরোক্ষ আক্রমণ—ছবির মতো পরিষ্কার।
ইমোজি নিয়ে এই নতুন বিতর্ক দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়েছে, কারণ জেন জি প্রজন্মের যেকোনো ঘোষণাই দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। তবে এই খবরটি আসলে অনলাইন যোগাযোগের বিপদ সম্পর্কে একটি সতর্কবার্তাও বটে।
কেউ হয়তো দ্বি-মুখী অর্থ বহন করা ‘👍’ ইমোজি দিয়ে ‘হ্যাঁ’ বা ‘দারুণ’ বলতে চেয়েছেন, কিন্তু অন্যজন সেটাকে নেতিবাচক অর্থেও ধরে নিতে পারে। ভিন্ন প্রজন্মের ইন্টারনেট ব্যবহারকারীরা একই ভাষা ব্যবহার করেও একে অপরের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন অর্থ বুঝতে পারছে।
ইমোজি (জাপানি শব্দ ‘এ’ অর্থাৎ ছবি এবং ‘মোজি’ অর্থাৎ অক্ষর থেকে উদ্ভূত) তৈরি করা হয়েছিল ডিজিটাল মাধ্যমে হওয়া কথোপকথনে কিছুটা মানবতা আর আবেগ যোগ করার জন্য। এর উদ্দেশ্য ছিল সাদামাটা লেখার জগতে এক ঝলক উষ্ণ রঙের ছোঁয়া আনা।
ইমোজি সবার জন্য উন্মুক্ত, যে কেউ এটি ব্যবহার করতে পারে। যেকোনো গোষ্ঠী এর নিজস্ব অদ্ভুত অর্থও তৈরি করতে পারে। কিন্তু এই অস্পষ্টতা অনেক সময় উত্তেজনাও তৈরি করে।
তাহলে প্রশ্ন হলো, ইমোজি কি আমাদের যোগাযোগকে উন্নত করেছে, নাকি বিশৃঙ্খলা বাড়িয়েছে? যদি ইমোজি সবার হয়েও কারও একার না হয়, তবে এর আসল অর্থ কে ঠিক করে দেবে?
কিথ হিউস্টন তাঁর ‘ফেস উইথ টিয়ার্স অফ জয়: এ ন্যাচারাল হিস্ট্রি অফ ইমোজি’ বইতে লিখেছেন, ইমোজিকে ঠিক ভাষা বলা যায় না, বরং এরা হলো ‘ভাষার ভেতরে থাকা বিদ্রোহী’। তিনি দারুণভাবে ব্যাখ্যা করেছেন যে, ইমোজি হলো ইন্টারনেটের ‘লিঙ্গুয়া ফ্রাঙ্কা’ বা সার্বজনীন ভাষা, আর এর আজকের অবস্থানে পৌঁছানোর পথচলাটা আপনার ধারণার চেয়েও অনেক বেশি জটিল। এর পূর্বসূরিরা অনেক প্রাচীন (যেমন: মিশরীয় হায়ারোগ্লিফ, চীনা অক্ষর, মেসোআমেরিকান লিপি), যদিও এর আধুনিক জন্ম জাপানে। সেখান থেকে এর বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে পড়ার যাত্রাটা ছিল খুবই দ্রুত, কিন্তু মসৃণ নয়।
হিউস্টন নিজেও এই ‘প্রাণবন্ত, জীবন্ত ইমোজি-🤗’ টি বেশ আগ্রহ নিয়েই ব্যবহার করেন। তবে তিনি এটাও মনে করিয়ে দেন যে, এগুলোর বহুমুখী ব্যবহারের আশীর্বাদের পাশাপাশি অভিশাপও রয়েছে। তিনি ইমোজিকে বলেছেন, ‘এক রঙিন ভাইরাস, যার লক্ষণগুলো আমরা এখনও পুরোপুরি বুঝে উঠতে পারিনি। 🦠’
ইমোজির এই অস্পষ্টতাই এর সবচেয়ে বড় সুবিধা এবং অসুবিধা। এর নমনীয়তার একটি লক্ষণ হলো, কেউ এখনও একমত হতে পারেনি যে ইমোজিকে ঠিক কোন শ্রেণিতে ফেলা উচিত। ভাষাবিদরা এর জন্মলগ্ন থেকেই এ নিয়ে বিতর্ক করে আসছেন। ২০১৫ সালে অক্সফোর্ড ইংলিশ ডিকশনারি যখন ‘😂’-কে ‘বর্ষসেরা শব্দ’ হিসেবে ঘোষণা করে, তখন ইমোজি ভাষার মর্যাদা পাওয়ার একটি পরোক্ষ স্বীকৃতি পায়। কিন্তু ইমোজি কি আসলেই ভাষা? এ বিষয়ে বেশিরভাগের মত হলো ‘🤔’।এটি যেন ভাষার মতো, কিন্তু ঠিক ভাষা নয়।এদিকে হিউস্টন বলেছেন, একে ‘বডি ল্যাঙ্গুয়েজ’ বা শারীরিক ভাষার মতো করে ভাবা যেতে পারে।
ইমোজি কি যতিচিহ্ন হিসেবেো কাজ করতে পারে (❣️🤡😬🔥)? অনেকের মতে এগুলোকে কৌশলপূর্ণভাবে এবং অস্পষ্টভাবে কথোপকথন শেষ করার একটি উপায় হিসেবে দেখা ভালো।
এই সংজ্ঞার জটিলতা থেকে বেরিয়ে হিউস্টন আমাদের ইমোজির জন্মের সেই সমৃদ্ধ গল্প বলেছেন। আজকের পরিচিত ইমোগুলোর কৃতিত্ব সাধারণত জাপানি ইঞ্জিনিয়ার শিগেতাকা কুরিতাকে দেওয়া হয়। ১৯৯৯ সালে তাঁর ডিজাইন করা কিছু ছবি জাপানের প্রধান মোবাইল পরিষেবা ব্যবহারকারীদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে (বিশেষ করে কিশোরদের কথা ভেবে এগুলো তৈরি করা হয়েছিল)।
তবে ইমোজির জন্ম নিয়েও বিতর্ক আছে। কে প্রথম ইমোজি তৈরি করেছে, তা নিয়ে আরও দাবিদার রয়েছে। অন্যান্য অনেক প্রযুক্তির মতোই এটিও বিকশিত হয়েছে—কিছুটা আকস্মিকভাবে আর কিছুটা ইচ্ছাকৃতভাবে। জাপানের মাঙ্গা ও অ্যানিমের মতো অনন্য নান্দনিক ঐতিহ্যগুলো ইমোজির মাধ্যমে বিশ্বজনীন রূপ পেয়েছে। ডিজিটাল চ্যাটিং জনপ্রিয় হওয়ার সাথে সাথে ইমোজির ব্যবহারও রকেটের গতিতে বাড়তে থাকে। অ্যাপল, গুগল-এর মতো প্রযুক্তি দানবরা ইমোজিকে তাদের সিস্টেমে যুক্ত করার পর এটি আর কোনো দেশের সীমানায় আটকে থাকেনি।
২০১১ সালে, ইউনিকোড কনসোর্টিয়াম নামে একটি অলাভজনক সংস্থা আনুষ্ঠানিকভাবে ইমোজির তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব নেওয়ার এক বছর পর, অ্যাপল তাদের মার্কিন বাজারের আইফোনে একটি ইমোজি কি-বোর্ড যুক্ত করে। আর তখন থেকেই মেসেজে হার্ট, পার্টি পপার আর সূর্য-হলুদ হাসিমুখের ছড়াছড়ি শুরু হয়।
২০১৩ সালে ইমোজিপিডিয়া ওয়েবসাইট চালু হয়, যার লক্ষ্য ছিল সমস্ত ইমোজির একটি সম্পূর্ণ ক্যাটালগ তৈরি করা। ২০১৪ সালে একটি সাইটে একটি আবেদন শুরু হয়: ‘টাকো ইমোজি চাই।’ ৩০,০০০-এর বেশি মানুষ সই করার পর জন্ম নিল ‘🌮’ ইমোজি। আর এই বিপ্লবের অনুঘটক ছিল ফাস্ট-ফুড চেইন ‘টাকো বেল’। কিন্তু দুই বছর পর, এক প্রবন্ধে এই ‘🌮’ ইমোজির একটি নতুন অর্থ ‘জননাঙ্গ’ প্রকাশ পায়, যা এর কর্পোরেট পৃষ্ঠপোষকরা হয়তো দুঃস্বপ্নেও কল্পনা করেননি।
ইমোজি পুরোপুরি ভাষা না হয়েও একটি ভাষার মতো, ধীরে ধীরে বিশ্বের ভাষাগত এবং বাণিজ্যিক পরিকাঠামোর অংশ হয়ে ওঠে। মানুষ আনন্দ (👏🎉😂), দ্বিধা (😑🤔🌤️), রসিকতা (😜) এবং প্রেম (😍😉) প্রকাশ করতে ইমোজি ব্যবহার করতে শুরু করে। এগুলো কোনো কিছুই সুনির্দিষ্টভাবে বলত না, আর ঠিক একারণেই এগুলো দিয়ে অনেক কিছু প্রকাশ করা যেত: উৎসাহ, ব্যঙ্গ, রাগ, বা মজা।
১৯৯১ সালে প্রতিষ্ঠিত ইউনিকোড কনসোর্টিয়াম সংস্থাটির কাজ ছিল ইন্টারনেট জুড়ে অক্ষর, সংখ্যার মতো স্থির চিহ্নগুলোর জন্য কোডিং-এর সামঞ্জস্য বজায় রাখা। কিন্তু এখন তাদের কাঁধে গতিশীল এই ইমোজি তত্ত্বাবধানের বিশাল দায়িত্ব এসে পড়ে।
নতুন ইমোজি অনুমোদনের দরজা ছিল এই কনসোর্টিয়াম। সাধারণ মানুষ নতুন আইকনের জন্য আবেদন করতে পারত, কিন্তু প্রযুক্তিবিদদের একটি দলই ছিল সেই দরজার দ্বাররক্ষক। তারাই আবেদনগুলো পর্যালোচনা করে সিদ্ধান্ত নিত কোন ছবি যোগ করা হবে আর কোনটি হবে না। ঠিক যেমন, কনডম ইমোজির আবেদন বাতিল হয়ে যায়।
কিন্তু এই প্রক্রিয়া নিয়ে সমালোচনাও কম হয়নি। প্রথমদিকে, ‘পেশা’ বোঝাতে শুধু পুরুষের ছবি ছিল। ‘দম্পতি’ মানে ছিল একজন পুরুষ ও একজন নারী। নারীর জুতো বলতে ছিল একটি লাল হাই-হিল। খাবারের ইমোজিগুলোতে জাপানি ও মার্কিন প্রভাবই বেশি ছিল, যা এর বিশ্বজনীন গল্পকে তুলে ধরতে পারত না।
ব্যবহারকারীদের চাপে ইউনিকোড কনসোর্টিয়াম পরে অনেক নতুন ইমোজি যোগ করে। ২০১৫ সালে তারা মানুষের ছবির জন্য পাঁচটি ভিন্ন ‘বাস্তবসম্মত’ ত্বকের রঙের অপশন চালু করে। কিন্তু এতে নতুন সমস্যা তৈরি হয়। আগে যে হলুদ রংটিকে বর্ণ-নিরপেক্ষ মনে করা হতো (যেমন ক্লাসিক স্মাইলি ফেস, লেগো মিনি-ফিগার বা সিম্পসনস কার্টুন), এখন সেটিকে কেউ কেউ বর্ণবাদী বলে মনে করতে শুরু করে। এমনকি ফর্সা ত্বকের রঙের ব্যবহারকেও কেউ কেউ ‘শ্বেতাঙ্গ আধিপত্যের’ প্রতীক হিসেবে দেখতে শুরু করে।
কনসোর্টিয়ামের ইমোজি সাবকমিটি—হিউস্টনের ভাষায় ‘ইমোজি সামলানোর দল একেবারে হিমশিম খাচ্ছিল। বিশেষ করে লিঙ্গ সমতার বিষয়টি ছিল খুবই চ্যালেঞ্জিং। পরে সমকামী দম্পতি, সমকামী অভিভাবক এবং নারীদের জন্য ১৬টি নতুন পেশার ইমোজি (পুরুষ ও নারী উভয় সংস্করণেই) যোগ করা হয়। ২০১৭ সালে লিঙ্গ-কেন্দ্রিক এই ইমোজিগুলো কোনো রাজনৈতিক বিতর্ক ছাড়াই গৃহীত হয়, যা হিউস্টনকে অবাক করেছিল। তবে সে বছর ফ্যান্টাসি চরিত্রগুলোর মধ্যে তখনও পুরুষকেন্দ্রিকতা দেখা গিয়েছিলো (🧙🧚🧛🧜🧞)।
এখন ইউনিকোডের ইমোজির পাশাপাশি বিভিন্ন প্ল্যাটফর্মের নিজস্ব স্টিকার, বিটমোজি বা মেমোজি রয়েছে, যা ব্যবহারকারীরা নিজেদের মতো করে তৈরি করতে পারে। অ্যাপলের জেনমোজি-র মতো নতুন প্রযুক্তি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার করে আরও হাজারো নতুন ইমোজি তৈরি করছে।
পুরোনো ইমোজির অর্থও প্রতিনিয়ত পাল্টাচ্ছে। যেমন, 💀 (মাথার খুলি) এখন আর শুধু অসম্মতি বোঝায় না, হাসতে হাসতে মরে যাওয়ার মতো মজাও বোঝায়। 😭 (কান্না) এখন দুঃখের পাশাপাশি অতিরিক্ত হাসির কারণে চোখে জল আসাও বোঝাতে পারে।
তবে ইমোজি আমাদের সেই ভাষার বাধাগুলো অনেকটাই দূর করে দিয়েছে। এর অস্পষ্টতাই যেন এর টিকে থাকার শক্তি। ছবি হওয়ায় ইমোজিকে কখনও একটি অর্থে বেঁধে রাখা যায় না। নতুন ইমোজি আসা বন্ধ হয়ে গেলেও পুরোনো গুলোই নতুন নতুন অর্থ নিয়ে বিকশিত হতে থাকবে। আর আমাদেরকেও তাদের সাথে তাল মিলিয়ে বিকশিত হতে চ্যালেঞ্জ জানাবে।
হিউস্টনের বইটির নামকরণ যে ইমোজির নামে করা হয়েছে, সেই ‘আনন্দাশ্রুর মুখ’ (😂), দীর্ঘদিন ধরে বিশ্বের সবচেয়ে জনপ্রিয় ইমোজি। কিন্তু সম্প্রতি জেন জি প্রজন্ম এর সম্পর্কেও নতুন রায় দিয়েছে: এই ‘😂’ ইমোজিটি এখন নাকি ‘ক্রিঞ্জ’ বা চরম বিরক্তিকর। এটি ব্যবহার করলে নাকি বোঝা যায়, প্রেরক একেবারেই সেকেলে।
আমি অভ্যাসের বশে এখনও এটি ব্যবহার করি। তবে এর আরেকটি কারণ হলো, আমার কাছে, ‘কুল’ হওয়ার চেয়ে আনন্দ করাটা সবসময়ই বেশি গুরুত্বপূর্ণ। আর আমার মতো কোটি কোটি মানুষ প্রতিদিন এই ‘😂’ ইমোজি একে অপরকে পাঠায়। ভবিষ্যতে হয়তো এর ব্যবহার কমে যাবে, এর প্রধান অর্থও বদলে যাবে। কিন্তু আপাতত, এটাই আমাদের সম্বল। আর এর কারণেই, আমরা বহু দূর থেকেও একসঙ্গে হাসতে পারি।


